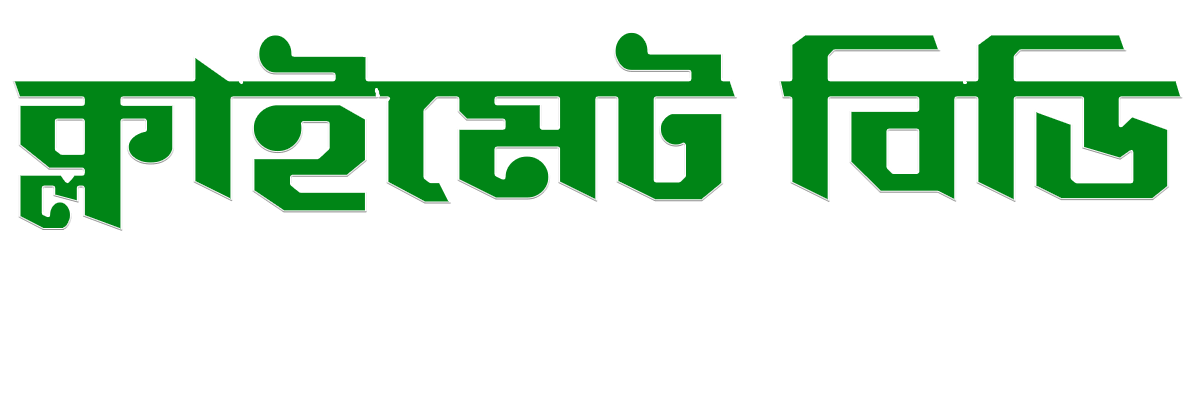বাংলাদেশ যখন জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি সবুজ ভবিষ্যতের দিকে এগোতে চাইছে, তখন নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিশেষ করে সৌরবিদ্যুৎ, আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। কিন্তু সম্প্রতি এই সম্ভাবনাময় খাতে এক ধরনের অনিশ্চয়তার মেঘ জমেছে। দরপত্র ছাড়া চুক্তি হওয়ার অভিযোগে গত বছর অন্তর্বর্তী সরকার বেসরকারি খাতের ৩১টি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্মতিপত্র (Letter of Intent) বাতিল করে দেয়। সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল
এই সিদ্ধান্তের ফলে কী প্রভাব পড়েছে? বিনিয়োগকারীরা কেন হতাশ? আর দেশের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি বা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ কেনই বা এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানাচ্ছে? চলুন, এই জটিল বিষয়টির প্রতিটি দিক সহজভাবে বিশ্লেষণ করি এবং বোঝার চেষ্টা করি, এর সাথে আমাদের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার লড়াই কতটা জড়িত। সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল
ঘটনার প্রেক্ষাপট: কী ঘটেছিল আসলে?
বিষয়টি বোঝার জন্য একটু পেছনে যেতে হবে। আগের সরকারের আমলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে ৩৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে সম্মতিপত্র দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ৩১টি ছিল বেসরকারি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলো থেকে প্রায় ৩,২৮৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি বিশাল পদক্ষেপ।
কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার স্বচ্ছতার প্রশ্ন তুলে দরপত্র ছাড়া দেওয়া এই সম্মতিপত্রগুলো বাতিল করে দেয়। সরকারের যুক্তি ছিল, প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়া কোনো প্রকল্প অনুমোদন করা উচিত নয়। আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানানোর মতো মনে হলেও, এর পেছনের গল্পটা আরও জটিল। সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল
সম্মতিপত্রের মূল্য: এটি কি শুধুই এক টুকরো কাগজ?
এখানেই মূল বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সিপিডির মতে, সম্মতিপত্র বা LOI হয়তো চূড়ান্ত চুক্তি নয়, কিন্তু এটি সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রেখেই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা একটি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ শুরু করেন।
সিপিডির উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী:
- বিশাল বিনিয়োগ: এই ৩১টি প্রকল্পের পেছনে এরই মধ্যে প্রায় ৩০ কোটি মার্কিন ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে।
- জমি ক্রয়: ১৫টি কোম্পানি সরকারের সম্মতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি কিনে ফেলেছে।
- বিনিয়োগ ফেরত পাওয়ার সুযোগ নেই: জমি কেনা, বিভিন্ন কর পরিশোধ এবং প্রাথমিক অবকাঠামো তৈরিতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা ফেরত পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। জমি বিক্রি করা কেনার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন একটি প্রক্রিয়া।
এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা, বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এক বিরাট আস্থার সংকটে পড়েছেন। তাদের বার্তা পরিষ্কার: সরকার পরিবর্তন হলেই যদি নীতি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা ঝুঁকিপূর্ণ।
চীনের বিনিয়োগ এবং আস্থার সংকট
এই বাতিল হওয়া প্রকল্পগুলোর মধ্যে চারটি প্রকল্পে চীনের সরাসরি বিনিয়োগ রয়েছে, যার দুটি প্রকল্পে শতভাগ মালিকানাই চীনা কোম্পানির। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চীন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাদের আস্থা হারানো মানে শুধু এই প্রকল্পগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নয়, বরং ভবিষ্যতে অন্যান্য খাতেও চীনা বিনিয়োগ আসার পথ সংকুচিত হয়ে যাওয়া।
বিনিয়োগকারীরা বলছেন, সরকার একদিকে নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সম্মেলন করছে, অন্যদিকে যারা এরই মধ্যে দেশে বিনিয়োগ করেছে, তাদের গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই দ্বিমুখী নীতি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি আনাকে আরও কঠিন করে তুলবে।
সিপিডির সুপারিশ: স্ববিরোধিতা নাকি বাস্তববাদী সমাধান?
অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, যে সিপিডি সবসময় দরপত্র ছাড়া চুক্তির বিরোধিতা করে এসেছে, তারা এখন কেন এই প্রকল্পগুলো পুনর্বিবেচনার কথা বলছে?
সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এর একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে মূল বিষয় হলো সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ হয়ে গেছে। তাই ঢালাওভাবে সব বাতিল না করে বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা উচিত।
তাদের প্রস্তাব স্ববিরোধী নয়, বরং একটি বাস্তবসম্মত সমাধান:
- পর্যালোচনা, হুবহু বাস্তবায়ন নয়: সিপিডি বলছে না যে আগের নির্ধারিত দামেই চুক্তি করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে একটি যৌক্তিক ও প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- অগ্রাধিকার প্রদান: যেসব কোম্পানি প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে (যেমন জমি কিনেছে), তাদের পুনরায় আবেদন করতে বলা যেতে পারে এবং সরকার তাদের অগ্রাধিকার দিতে পারে।
- তদন্ত কমিটি গঠন: ৩৭টি প্রকল্পের সবগুলোই রাজনৈতিক বিবেচনায় বা দুর্নীতি করে অনুমোদন পায়নি। কোন প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে, তা খুঁজে বের করতে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ঢালাওভাবে সব বাতিল করা अन्याय।
এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা যেমন ফিরবে, তেমনি সরকারের স্বচ্ছতার নীতিও বজায় থাকবে।
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে এর প্রভাব কী?
এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আমাদের পরিবেশ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভবিষ্যৎ। যখন পুরো বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসছে, তখন আমাদের সৌরবিদ্যুতের মতো একটি সম্ভাবনাময় খাতকে এগিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
যদি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারিয়ে ফেলে, তবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নতুন প্রযুক্তি এবং বড় বিনিয়োগ আসা কঠিন হয়ে পড়বে। সরকার নতুন করে দরপত্র ডেকেও আশানুরূপ সাড়া পাচ্ছে না, যা এই আস্থার সংকটকেই প্রমাণ করে। এর ফলে আমাদের ক্লিন এনার্জি বা পরিচ্ছন্ন জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে আমাদের পরিবেশের জন্য একটি অশনিসংকেত।
শেষ কথা
৩১টি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্মতিপত্র বাতিলের বিষয়টি এখন একটি জটিল নীতিগত বিতর্কে পরিণত হয়েছে। একদিকে রয়েছে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার তাগিদ, অন্যদিকে রয়েছে বিনিয়োগকারীদের আস্থা রক্ষা এবং দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চ্যালেঞ্জ।
সিপিডি এবং বিনিয়োগকারীদের প্রস্তাবিত পথ—অর্থাৎ, ঢালাওভাবে বাতিলের পরিবর্তে একটি পর্যালোচনার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক সমাধান খুঁজে বের করা—একটি মধ্যমপন্থা হতে পারে। সরকারের উচিত হবে এই বিষয়ে দ্রুত একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা। কারণ স্থিতিশীল নীতি এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ছাড়া একটি সবুজ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ভবিষ্যৎ এবং পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে আমরা কতটা সফল হব।
আপনার মতামত কী?
আপনি কি মনে করেন সরকারের এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, নাকি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে এটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত? নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? আপনার মূল্যবান মতামত নিচে কমেন্ট করে জানান।
পরিবেশগত নীতি এবং সবুজ বিনিয়োগের জটিলতা নিয়ে কাজ করছেন? আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বা কৌশলগত দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হলে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। একটি টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আমরা আপনার পথচলার সঙ্গী হতে পারি।