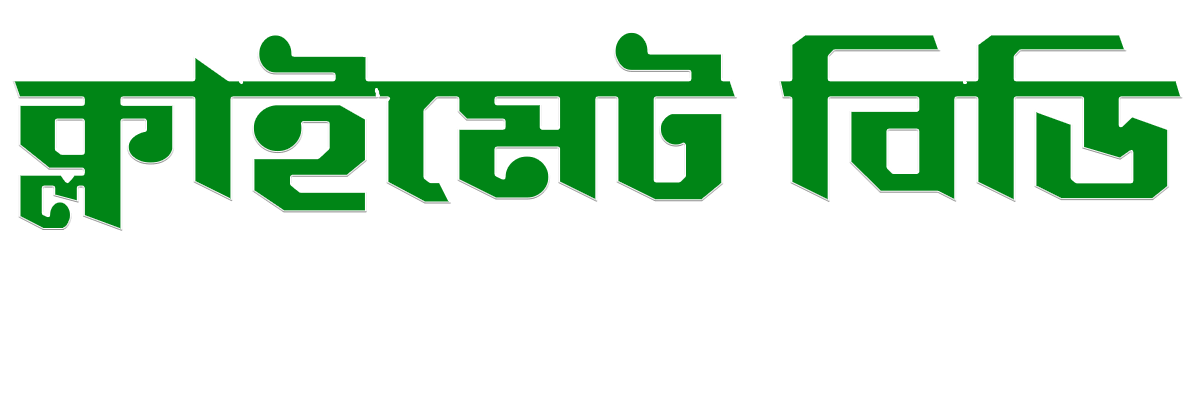একটু ভাবুন তো, কাঠফাটা রোদে ক্লান্ত শরীর নিয়ে আপনি একটু ছায়া খুঁজছেন। কিছুদিন আগেও যেখানে সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে থেকে আপনাকে প্রশান্তি দিত, আজ সেখানে কংক্রিটের সড়ক বিভাজক আর কিছু বাহারি ফুলের চারা। সৌন্দর্য হয়তো বেড়েছে, কিন্তু খাঁ খাঁ রোদে পোড়া পিঠটাকে জুড়ানোর সেই শীতল আশ্রয়টুকু হারিয়ে গেছে। কোথায় গেল ১৩ লাখ গাছ
এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত, এটিই এখন বাংলাদেশের উন্নয়নের এক রূঢ় বাস্তবতা। উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে আমরা যে মূল্য দিচ্ছি, তা আমাদের পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অশনি সংকেত। কোথায় গেল ১৩ লাখ গাছ
যে পরিসংখ্যান আমাদের ভাবিয়ে তুলবে
সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে এক চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। গত ২৬ মাসে, অর্থাৎ ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, সারা দেশে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কারণে প্রায় ১৩ লাখ গাছ কাটা হয়েছে। সংখ্যাটা আরেকবার পড়ুন—তেরো লাখ!
বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক যখন আমরা দেখি, এই বৃক্ষনিধনের হার কমছে না, বরং চলমান রয়েছে। গবেষণা বলছে, প্রথম ১২ মাসে (মার্চ ‘২৩ – মার্চ ‘২৪) কাটা হয়েছিল প্রায় সাড়ে ১১ লাখ গাছ। আর পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ শুধু ২০২৪ সালের প্রথম দিকেই কাটা হয়েছে প্রায় পৌনে দুই লাখ গাছ। এই পরিসংখ্যান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, উন্নয়নের নামে আমরা কতটা দ্রুত আমাদের সবুজ আচ্ছাদনকে ধ্বংস করে চলেছি।
গাছ কাটার এই মিছিলে সবচেয়ে এগিয়ে আছে খুলনা জেলা, যেখানে এক বছরেই প্রায় ৮৫ হাজার গাছ কাটা হয়েছে। এরপরই রয়েছে লক্ষ্মীপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও যশোরের মতো জেলাগুলো। এমনকি দেশের ফুসফুস বলে পরিচিত এলাকাগুলোতেও চলছে এই সবুজ ধ্বংসের উৎসব। কোথায় গেল ১৩ লাখ গাছ
উন্নয়ন বনাম পরিবেশ: এক অসম লড়াই
শহরের সৌন্দর্যবর্ধন, দ্রুতগতির উড়ালসড়ক নির্মাণ, মেট্রোরেলের স্থাপনা কিংবা নদীর বেড়িবাঁধ তৈরি—কারণগুলো নিঃসন্দেহে জনগুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই প্রকল্পগুলো কি গাছ বাঁচিয়ে করা যেত না?
ঢাকার কথাই ধরা যাক। পান্থকুঞ্জ পার্ক বা ফার্মগেট এলাকার শহীদ আনোয়ারা পার্কের মতো সবুজে ঘেরা স্থানগুলো আজ কংক্রিটের নিচে চাপা পড়েছে। মেট্রোরেল বা উড়ালসড়ক আমাদের যাতায়াতকে সহজ করবে, কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা হারিয়ে ফেলছি শহরের অক্সিজেন ফ্যাক্টরিগুলো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে, প্রকল্পের কাজ শেষে পার্কগুলো পুনঃস্থাপন করা হবে। কিন্তু একটি শতবর্ষী গাছের ছায়া কি কয়েকটি চারাগাছ রাতারাতি ফিরিয়ে দিতে পারে?
একই চিত্র খুলনার কয়রা উপজেলায়। নদীর পাড় রক্ষায় বেড়িবাঁধ জরুরি, কিন্তু তার জন্য একবারে ৫০ হাজার গাছ কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক ছিল? সমালোচনার মুখে গাছ লাগানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এক বছরে তার কোনো বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। কর্মকর্তাদের ভাষ্য, “বাঁধের কাজ শেষ না হলে গাছ নষ্ট হবে।” এই যুক্তি আমাদের আরেকটি গভীর সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে—প্রকল্পের নকশায় পরিবেশগত চিন্তার চূড়ান্ত অভাব।
সড়ক নির্মাণ, পানি উন্নয়ন, বন গবেষণা, এমনকি কৃষি গবেষণার মতো ১২টিরও বেশি সরকারি সংস্থার নাম উঠে এসেছে এই বৃক্ষনিধনের তালিকায়। এটি প্রমাণ করে, সমস্যাটি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিভাগ নয়, বরং এটি একটি পদ্ধতিগত সংকট।
সমন্বয়হীনতার দুষ্টচক্র এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উন্নয়নের প্রয়োজনে গাছ কাটার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু যে হারে গাছ কাটা হচ্ছে, সে হারে কি রোপণ করা হচ্ছে? আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, প্রকল্পের নকশা করার সময়ই কেন গাছগুলোকে রক্ষা করার কথা ভাবা হচ্ছে না?
এর উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যকার সমন্বয়হীনতায়। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের প্রকল্পের জন্য গাছ কাটার বিষয়টি পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে জানায়ই না। প্রকল্প প্রস্তাবের সময় গাছ বাঁচিয়ে কীভাবে নকশা করা যায়, সেই বিকল্প পথ তারা দেখায় না। ফলে, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব যাদের, তারাই থেকে যায় অন্ধকারে।
এই অপরিকল্পিত বৃক্ষনিধন আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। যখন বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে, শহরগুলো ‘হিট আইল্যান্ড’-এ পরিণত হচ্ছে, তখন গাছই আমাদের একমাত্র প্রাকৃতিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রক। একটি বড় গাছ শুধু ছায়া দেয় না, এটি বাতাসের তাপমাত্রা কমায়, দূষণ শোষণ করে এবং বৃষ্টির পানি ধরে রেখে মাটিকে উর্বর রাখে।
আজকের এই ১৩ লাখ গাছ কাটার অর্থ হলো, ভবিষ্যতে আরও বেশি গরম, আরও ঘন ঘন আকস্মিক বন্যা এবং আরও দূষিত বাতাসের জন্য প্রস্তুত হওয়া। এটি আমাদের পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের উপর একটি সরাসরি আক্রমণ।
শেষ কথা: আমাদের কী করণীয়?
উন্নয়ন অপরিহার্য, কিন্তু সেই উন্নয়ন যদি হয় আত্মঘাতী, তবে তা অর্থহীন। আমাদের এমন একটি টেকসই মডেলে যেতে হবে, যেখানে উন্নয়ন এবং পরিবেশ একে অপরের প্রতিপক্ষ নয়, বরং পরিপূরক।
এর জন্য প্রয়োজন:
- যেকোনো প্রকল্পের শুরুতেই পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) বাধ্যতামূলক করা এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলা।
- প্রকল্পের নকশায় গাছপালা ও সবুজ এলাকাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।
- একটি গাছ কাটার আগে অন্তত দশটি গাছ লাগানোর নীতি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় তৈরি করা, যেখানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রাখা হবে।
এই ১৩ লাখ গাছের নীরব কান্না যদি আমাদের বিবেককে নাড়া না দেয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে এক ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয়ের জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।
আপনার মতামত কী?
উন্নয়ন ও পরিবেশের এই দ্বন্দ্বে আপনি কোনটিকে এগিয়ে রাখবেন? আপনার এলাকার এমন কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে আমাদের সাথে শেয়ার করুন।
আপনি যদি পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলা বা টেকসই প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি হন, তবে আসুন, আমরা একটি সবুজতর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একযোগে কাজ করি। আপনার পরিকল্পনা ও ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।