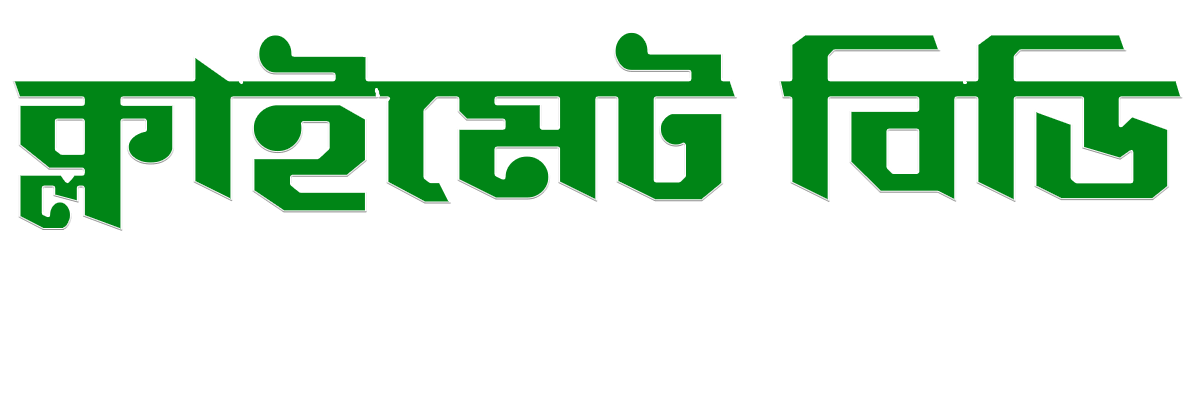বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন—নামটা শুনলেই চোখে ভাসে স্বচ্ছ নীল জল, সারি সারি নারকেল গাছ আর দিগন্তজোড়া আকাশ। এই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের টানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক ছুটে যান সেখানে। কিন্তু আমাদের এই ভালোবাসাই যেন দ্বীপটির জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন, প্লাস্টিক বর্জ্য আর পরিবেশগত অবহেলার কারণে দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপটি আজ অস্তিত্ব সংকটে।
তবে আশার কথা হলো, এই মরতে বসা দ্বীপটিকে বাঁচাতে সরকার এবার একটি ব্যাপক ও সমন্বিত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আর এই পরিকল্পনার সবচেয়ে আলোচিত অংশ হলো—সেন্ট মার্টিনে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের উপর ‘পরিবেশ সংরক্ষণ ফি’ আরোপ।
এই ঘোষণা শোনার পর অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে: এটা কি পর্যটকদের ওপর আরও একটি করের বোঝা, নাকি দ্বীপটিকে বাঁচানোর সত্যিকারের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ? চলুন, এই পরিকল্পনার গভীরে গিয়ে এর ভালো-মন্দ দিকগুলো বিশ্লেষণ করা যাক।
ফি’র নেপথ্যে কী: নিছক করের বোঝা না রক্ষার বর্ম?
প্রথমেই আসা যাক এই ‘পরিবেশ সংরক্ষণ ফি’-এর কথায়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানিয়েছেন, এই ফি সংগ্রহ করবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এবং এর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হবে দ্বীপটির পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার কাজে।
অনেকেই হয়তো ভাবছেন, সেন্ট মার্টিনে যাওয়ার খরচ তো এমনিতেই অনেক বেশি, এর উপর আবার নতুন ফি কেন? কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে এর পেছনের যুক্তিটা স্পষ্ট হয়। একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের ওপর যে অনেক চাপ পড়ে, তার একটি মূল্য আছে। এই ফি সেই মূল্যের একটি প্রতীকী স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে প্রতিটি পর্যটককে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, এই দ্বীপের সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি তা রক্ষা করারও একটি দায়িত্ব তাদের রয়েছে।
তবে আসল পরীক্ষা হবে এই আদায়কৃত অর্থের সঠিক ব্যবহারে। যদি এই টাকা দিয়ে সত্যিই দ্বীপের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়, সৈকতে সাগরলতা ও কেয়া বন তৈরি করে জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা হয়, এবং দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে এই ফি একটি ‘করের বোঝা’ না হয়ে দ্বীপের জন্য একটি ‘রক্ষার বর্ম’ হয়ে উঠবে।
শুধু ফি নয়, রয়েছে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা
এই উদ্যোগের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো, সরকার শুধু ফি আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এর পেছনে রয়েছে একটি সুদূরপ্রসারী এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যা সেন্ট মার্টিনের সংকটকে বিভিন্ন দিক থেকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে।
১. স্থানীয় মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থান:
সেন্ট মার্টিনের প্রায় ১০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা পর্যটনের ওপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল। পর্যটন নিয়ন্ত্রিত হলে তাদের জীবিকার কী হবে—এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটি তিন বছর মেয়াদি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৫০০টি পরিবারকে হাঁস-মুরগি পালন, চিপস তৈরি ও কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলেদের জন্য সহায়তার পরিমাণও বাড়ানো হবে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও টেকসই করবে এবং পর্যটনের ওপর একক নির্ভরশীলতা কমাবে।
২. প্লাস্টিকমুক্ত সেন্ট মার্টিন:
অক্টোবর মাস থেকে সেন্ট মার্টিনে সিঙ্গেল-ইউজ বা একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হতে চলেছে। এটি দ্বীপের পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। প্লাস্টিকের বোতল, প্যাকেট, স্ট্র—এগুলো শুধু দ্বীপের সৌন্দর্যই নষ্ট করে না, সমুদ্রের তলদেশে জমে প্রবাল ও সামুদ্রিক প্রাণীদেরও মারাত্মক ক্ষতি করে। এই সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হলে তা দ্বীপের চেহারাই পাল্টে দেবে।
৩. বৈজ্ঞানিক উপায়ে জোনিং:
সেন্ট মার্টিনকে চারটি জোনে ভাগ করার প্রস্তাবটি এই পরিকল্পনার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক।
- জোন-১ (মাল্টিপল ইউজ জোন): এখানে পরিবেশবান্ধব পর্যটন চলবে।
- জোন-২ (বাফার জোন): সংবেদনশীল এলাকাকে রক্ষা করবে।
- জোন-৩ (জীববৈচিত্র্য রক্ষা জোন): স্থানীয়রা শর্তসাপেক্ষে সম্পদ আহরণ করতে পারবে।
- জোন-৪ (কঠোর সংরক্ষণ জোন): এটি হবে একটি নো-গো এলাকা, যেখানে কোনো ধরনের প্রবেশাধিকার থাকবে না।
এই জোনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যে, দ্বীপের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ, যেমন প্রবালের আবাসস্থল বা কচ্ছপের ডিম পাড়ার জায়গাগুলো, মানুষের অবাধ বিচরণ থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট চাপের মুখে টিকে থাকার জন্য দ্বীপের ইকোসিস্টেমকে সাহায্য করবে।
ক্ষত যখন অনেক গভীরে
এই পরিকল্পনাগুলো কেন এত জরুরি, তা বোঝা যায় দ্বীপটির বর্তমান অবস্থা দেখলে। সভায় উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সমুদ্র থেকে লবস্টার প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হোটেলের সৌন্দর্য বাড়াতে গিয়ে এমন সব বিদেশি প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে, যা স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি। জাহাজের নোঙরের আঘাতে প্রতিনিয়ত প্রবাল প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
এই গভীর ক্ষত সারাতে হলে এমন কঠোর এবং সমন্বিত পদক্ষেপের কোনো বিকল্প নেই।
শেষ কথা: আশা ও চ্যালেঞ্জ
সব মিলিয়ে, সেন্ট মার্টিনকে বাঁচাতে সরকারের এই নতুন পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। এটি শুধু একটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়, বরং একটি বৈজ্ঞানিক, মানবিক ও পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।
তবে আসল চ্যালেঞ্জটি লুকিয়ে আছে এর সঠিক বাস্তবায়নের মধ্যে। পরিবেশ সংরক্ষণ ফি আদায়ে স্বচ্ছতা, প্লাস্টিক নিষেধাজ্ঞার কঠোর প্রয়োগ, জোনিং ব্যবস্থার তদারকি এবং স্থানীয় মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা—এই সবগুলো কাজ সফলভাবে করতে পারলেই সেন্ট মার্টিন আবার তার পুরনো রূপে ফিরতে পারবে।
এটি শুধু একটি দ্বীপ বাঁচানোর লড়াই নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য টেকসই পর্যটন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। এই পরীক্ষায় আমরা সফল হতে পারলে তা ভবিষ্যতের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।
আপনার মতামত কী?
সেন্ট মার্টিনের পরিবেশ রক্ষায় পর্যটকদের উপর ফি আরোপের এই সিদ্ধান্তকে আপনি কীভাবে দেখছেন? এই পরিকল্পনা সফল করতে আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? আপনার মূল্যবান মতামত নিচের কমেন্ট বক্সে জানান।
পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত এমন আরও বিশ্লেষণমূলক লেখা পড়তে আমাদের সাথেই থাকুন!